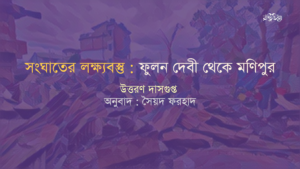
সংঘাতের লক্ষ্যবস্তু : ফুলন দেবী থেকে মণিপুর
সংঘাত নিয়ে স্থানীয় অথবা আন্তর্জাতিক- উভয়ক্ষেত্রেই জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গী থাকা খুব জরুরী, কারণ সংঘাত কৌশলের অংশ হিসেবে প্রায়ই নারীরা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন।
একটি রাষ্ট্রনৈতিক জার্নাল
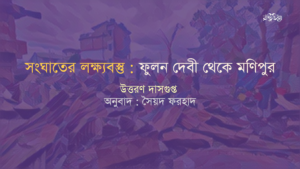
সংঘাত নিয়ে স্থানীয় অথবা আন্তর্জাতিক- উভয়ক্ষেত্রেই জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গী থাকা খুব জরুরী, কারণ সংঘাত কৌশলের অংশ হিসেবে প্রায়ই নারীরা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন।
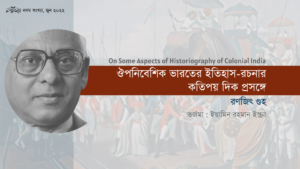
তর্জমা : ইয়ামিন রহমান ইস্ক্রা সম্পাদকের ভূমিকা প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ-র জন্ম তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বাকেরগঞ্জের সিদ্ধকাটি গ্রামে (বাকেরগঞ্জ উপজেলা বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় এবং সিদ্ধকাটি...
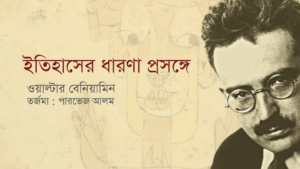
ইতিহাসের ধারণা প্রসঙ্গে-র প্রধান বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ঐতিহ্যের মধ্যে হাজির থাকা ইতিহাসের ধারণা। বেনিয়ামিনের আমলের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ঐতিহ্য বহন করা বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষগুলো সরল রৈখিক সময়ের মধ্য দিয়ে ক্রমশ প্রগতির দিকে এগিয়ে যাওয়া যেই ধরণের ইতিহাসবাদী চিন্তায় আটকে গিয়েছিল, তা এই লেখার সমালোচনার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু।

চারদশকের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ, নারীদের প্রতি বৈষম্য— এবং হঠাৎ করেই বাইশ বছর বয়সী একজন কুর্দি নারীর নিথর দেহ হয়ে উঠেছে জুলুমের এই সকল স্তরের প্রতীক।
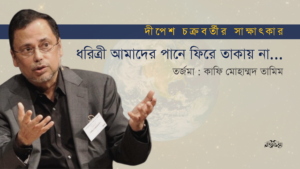
পৃথিবীর কাছে ও অন্য প্রাণীর কাছে মানুষের যে কী এবং কত পরিমাণে ঋণ, মানুষ যেন ভেবেছিল তা সম্পূর্ণ ভুলে মেরে দিয়েও নিজের ক্ষমতা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর মুনাফা অনির্দিষ্ট ভাবে বাড়িয়ে চলবে। এই সহজ কথাটাও মনে থাকে না, যে অক্সিজেন ব্যতীত আমরা বাঁচতামই না, তাও বাতাসকে জোগান দেয় নানান ‘মনুষ্যেতর’ প্রাণী, এবং এই পৃথিবী গ্রহটির নানান প্রক্রিয়া। এই ভুলে-যাওয়াটার প্রথম শুরু ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দিনগুলোতে, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সূচনায়। তার পর সেই পশ্চিম-প্রদর্শিত পথে অন্যান্য দেশের নেতারাও হেঁটেছেন।
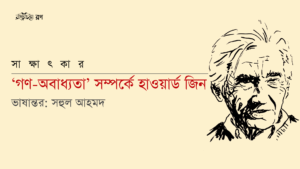
মানুষ দুই কারণে অন্যায় অবিচারের কাছে নতি স্বীকার করে: একটি হলো তারা এটাকে অন্যায়-অবিচার হিসেবে ঠাহর পারে না। একজন যুবক সামরিক বাহিনীকে যোগ দিতে পারে এইটা না জেনেই যে তাকে এমন একটা যুদ্ধে যোগ দিতে হতে পারে যা নৈতিকভাবে ন্যয়সঙ্গত নয়।

আমার বিশ্বাস, আমার বইয়ের বার্তাটি এসময়ে বেশি প্রাসঙ্গিক। কেননা শুধুমাত্র ভাইরাস-ই সংক্রামক নয়, আমাদের ব্যবহারও তাই। যদি আমরা ধরে নিই, বেশিরভাগ মানুষ প্রকৃত অর্থেই স্বার্থপর এবং এর ভিত্তিতে এই ভাইরাসকে মোকাবেলা করতে চাই, তবে মানুষের মাঝেও আমরা এটার প্রকাশ দেখতে পাবো। কিন্তু যদি আমরা ভাবি, বেশিরভাগ মানুষ একে অপরের পাশে দাঁড়াতে চায় এবং তারা অন্যকে সাহায্য করতে চায়, কেবল তখনই আমরা মানুষকে উৎসাহিত করতে পারব। এটা কিছুটা চটকদার শোনালেও দয়া বা পরোপকারিতা যে আসলেই সংক্রামক সে ব্যাপারে বহু মনস্তাত্ত্বিক প্রমাণাদি আছে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে এগুলো ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি আপনি যাদেরকে চেনেন না, কখনো দেখেননি তাদেরকেও অনুপ্রাণিত করে।
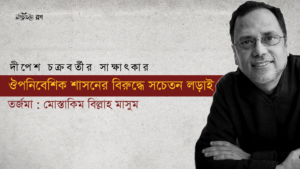
আধুনিকতা বেশ দুরূহ ও জটিল একটি শব্দ, কিন্তু এই আলোচনার সুবিধার্থে আধুনিকতাকে আমরা কান্টের জনপরিসরে যুক্তি প্রয়োগের ধারণাতেই সীমাবদ্ধ রাখছি। এখন একবার যখন আপনি আধুনিকতার ছাঁচে গড়ে উঠলেন, তখন প্রাক-আধুনিক সম্পর্ক ও ধারণাসমূহের উপর ভিত্তি করে একটি জনজীবন বা নাগরিক জীবন নির্মাণ করা প্রায় অসম্ভব। ভারতে জাতপাতের ভিত্তিতে যেই জুলুম তার উদাহরণ দেয়া যায়।
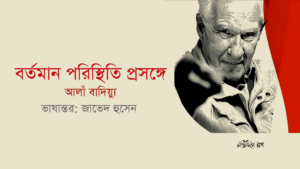
বিশ্বাস করুন, স্বল্প আর দীর্ঘমেয়াদি দুই রকমের এই লক্ষ্য জনপ্রিয় করার মাধ্যমে আমরা নতুন এক যুগের সূচনা করতে পারবো। এতক্ষণ যা নিয়ে কথা বললাম, সেই সব ‘সংগ্রাম’, এবং ‘আন্দোলন’ এবং ‘প্রতিবাদে’র নেতিবাচক দ্বান্দিকতা নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। সেই সাথে নিঃশেষ করছে আমাদের। এসব পার হয়ে আমরা হয়ে উঠতে পারব এক নতুন গণ কমিউনিজমের অগ্রদূত। মার্কসের মত করে বললে যার ‘ভূত’ আরও একবার শুধু ফ্রান্স বা ইউরোপ নয়, তাবৎ দুনিয়াকে তাড়িয়ে বেড়াবে।
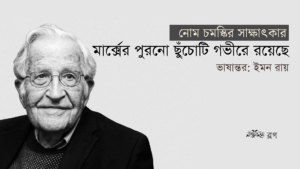
মানব সমাজ কোনো সংঘবদ্ধ আকারে বজায় থাকবে কিনা, অথবা আমরা অপরিবর্তনীয় খাদের কিনারে চলে গেছি কিনা এবং আমরা সম্পূর্ণ বিপর্যয়ে পতিত হয়েছি কিনা সে বিষয়ে এ প্রজন্মই সিদ্ধান্ত নেবে। আণবিক অস্ত্রের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির বেলায় একই প্রশ্নঃ এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। অন্যান্য সমস্যা রয়েছে। ব্যাপক ও অহেতুক জীবনের মূল্য দিয়ে কোনো একভাবে অতিমারীকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, কিন্তু আরও কিছু অপেক্ষা করছে।