
- ফ্লোরা সরকার
And contrary to the opinion of the masses, one’s true self, according to Socretes, is not to be identified with what we own with our social status, our reputation or even with our body. Instead, Socretes famously maintained that our true self is our soul – Academy of Ideas.
ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিক এরিক ফ্রমের “স্কেপ ফ্রম ফ্রিডাম বা ফিয়ার অফ ফ্রিডম” বইটির উপর আলোচনার আগে ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্সটিটিউট অফ সোশাল রিসার্চ, যা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল নামে পরিচিত, সেই সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেয়া যাক। ১৯২০ এর দশকের শুরুতে বাম, মধ্য ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে মতাদর্শগত প্রবল বিতর্কের পরিণতিতে ওয়াইমার জার্মানিতে বৌদ্ধিক জগতে প্রবল আলোড়ন ও র্যাডিকালাইজেশন ঘটেছিল। সেই সময়টা ছিল খুব দ্রুত সাংস্কৃতিক রূপান্তরের , পুরানো মূল্যবোধ ভাঙ্গনের এবং নতুন মূল্যবোধ অনুসন্ধানের সময়। এই গোটা প্রক্রিয়াটির সঙ্গে ফ্রয়েড, হেগেল, মার্কস ও হাইদেগারের তত্ত্বভাবনা এবং এক্সপ্রেশনিজম, ফেনোমেনোলজি বা বিষয়বিদ্যা ও অস্তিত্ববাদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। যেসব তরুণ বুদ্ধিজীবী পরবর্তীকালে ইন্সটিটিউট অফ সোশাল রিসার্চ বা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলে যোগদান করেছিলেন তারা সবাই এই তর্কবিতর্কের প্রবাহের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে হেগেলের দ্বাদ্বিক পদ্ধতি ও মার্কস কর্তৃক আরও উন্নয়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিকরা মনে করতেন , কোনো একটা তত্ত্ব কোন প্রশ্ন কিভাবে উত্থাপন করবে, কিভাবে তাকে সূত্রায়িত করবে, কিভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর দিবে – সেটার প্রধান নির্ধারক হলো তত্ত্বটার সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।
আমরা সবাই স্বাধীনতা চাই, কিন্তু স্বাধীনতাকে ভয়ও পাই। কারণ স্বাধীনতা মানুষকে তার দায়িত্ব থেকে পালাতে দেয়না, একইসঙ্গে আবার নিশ্চিত নিরাপত্তার অবসানও ঘটায়। এর পরিণতিতে মানুষ স্বাধীনতার দায়কে প্রত্যাখ্যান করে এবং কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এরিক ফ্রম মূলত একজন মনবিজ্ঞানী। জীবনের শুরুতে ছিলেন গোঁড়া ফ্রয়েডিয়ান, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি কারেন হরনি ও হ্যারি সুলিভানের সঙ্গে মনঃসমীক্ষণ বিদ্যার কালচারিস্ট বা সংস্কৃতিবাদী চিন্তাধারার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিত হন। ফিয়ার অফ ফ্রিডাম বইটিতে এরিক ফ্রম ফ্রিডম বা স্বাধীনতা বলতে মূলত ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বুঝিয়েছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে ফ্রমের মতামত হলো – পাশ্চাত্য রেনেসাঁ এবং পুঁজিবাদের হাত ধরে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা এসেছিল, সেটা ভুল ধারণা ছিল। আধুনিক মানুষ প্রাক-ব্যক্তিবাদী সমাজের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে ঠিকই, যেটা একইসঙ্গে তাকে কিছুটা নিরাপত্তা দিয়েছে এবং সীমাবদ্ধ করেছে, যে কারণে ধনাত্মক স্বাধীনতা অর্জন তার পক্ষে আজও সম্ভব হয় নাই। ধনাত্মক স্বাধীনতা বলতে ফ্রম বুঝিয়েছেন, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগমূলক এবং সংবেদনশীল বা ইন্দ্রিয়গত সম্ভাবনাগুলি অর্জন। স্বাধীনতা যদিও মানুষকে স্বনির্ভর ও যৌক্তিক প্রাণী হিসেবে গড়ে তুলেছে, একই সঙ্গে তাকে বিচ্ছিন্নও করেছে, যে কারণে মানুষ উদ্বিগ্ন ও ক্ষমতাহীন। এই বিচ্ছিন্নতার ভার অসহনীয়। যে কারণে তার সামনে দুটো পথ খোলা আছে – এক. হয় তাকে স্বাধীনতার এই অসহীয়তা থেকে তাকে পালিয়ে যেয়ে নতুন কোন নির্ভরতার জায়গা খুঁজতে হবে অথবা দুই. তাকে ধনাত্মক স্বাধীনতার খোঁজ করতে হবে, যা মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও অনন্যতার উপর নির্ভর করে। যে কারণে ফ্রম তার বই সম্পর্কে বলেছেন, বইটা যত না পূর্বাভাসমূলক তার থেকে অনেক বেশি সণাক্তকরণ বা অনুসন্ধানমূলক। সমাধানের চেয়ে বিশ্লেষণমূলক। বইটাকে তিনি প্রধানত সাতটা অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে প্রতিটা অধ্যায়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার জটিল গ্রন্থীগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের চেষ্টা করে গেছেন। আমরাও চেষ্টা করবো, ফ্রম কিভাবে এই বিশ্লেষণগুলি করেছেন সেটা দেখতে এবং বুঝতে।
প্রথম অধ্যায়ে স্বাধীনতা কোন মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা কিনা সেটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেহেতু ফ্রম একজন ইউরোপীয় লেখক, কাজেই ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি তার জায়গা থেকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তার বিশ্লেষণের যত গভীরে আমরা যাবো, আমরা দেখতে পাবো, ফ্রম উল্লেখিত স্বাধীনতার জটিল প্রবাহগুলি অ-ইউরোপীয় অর্থাৎ এশীয় ও অন্যান্য মহাদেশীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গেও অনেক মিলে যায়। অধ্যায়ের শুরুতেই ফ্রম বলছেন, আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু হলো, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিকল থেকে নিজেদের মুক্ত করা। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বলতে, ফ্রম এই বিষয়গুলির পেছনে যেসব কর্তৃত্ববাদ কাজ করে, সেই কর্তৃত্বকে বুঝিয়েছেন। ব্যক্তির মুক্তির জন্যে একে একে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র , ধর্মীয় স্বায়ত্বশাসন এবং ইন্ডিভিজুয়ালিজম বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ অর্জন করার জন্যে মানুষকে কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জনের জন্যে বাইরের শক্তির দমনপীড়নের অবলুপ্তি শুধু প্রয়োজনীয় একটা শর্তই নয়, অবশ্যম্ভাবী শর্ত। ব্যক্তিস্বাধীনতা শুধু ফ্যাসিজমের মাধ্যমেই কেড়ে নেয়া হয়না, অ্যান্টি-ফ্যাসিজমের মাধ্যমেও কেড়ে নেয়া হতে পারে। আমেরিকান দার্শনিক জন ডিউইর ‘ফ্রিডাম এ্যান্ড কালচার’ বই থেকে চমৎকার একটা মন্তব্য আমরা পাই, “গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে সব থেকে বড় যে হুমকির সম্মুখীন আমরা হই, সেটা কোন টোটালিটেরিয়ান স্টেট বা সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে নয়। হুমকিটা হলো নিজেদের মনমানসিকতা এবং নিজেদের গড়া প্রতিষ্ঠানের অবস্থা থেকে। যে অবস্থা ও মানসিকতা এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয় এনে দিয়েছে বিভিন্ন কর্তৃত্ববাদ, শৃঙ্খলা, অভিন্নতা এবং বিদেশি নেতাদের উপর নির্ভরতাকে। যে কারণে প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির মধ্যে একটা যুদ্ধাবস্থা সব সময় লেগে থাকে”। ফ্রমের মতে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়তে হলে এই বিষয়গুলি ভালো করে বুঝতে হবে এবং সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা, যা ফ্যাসিজম বা স্বৈরতন্ত্রকে গড়ে ঊঠতে সাহায্য করে।

ব্যক্তির জায়গা থেকে স্বাধীনতা, অনুগত হবার আকাঙ্খা এবং ক্ষমতার জন্যে লালসা ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রম কিছু চমৎকার প্রশ্ন তুলেছেন : ব্যক্তির অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে স্বাধীনতা বলতে আমরা প্রকৃতপক্ষে কি বুঝে থাকি? ব্যক্তির ভেতরে স্বাধীনতার আকাঙ্খা কি আগে থেকেই তার স্বভাবের মধ্যে থাকে? স্বাধীনতার এই বোধ কি সব সমাজে একইভাবে দেখা যায় নাকি সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়? স্বাধীনতা বলতে কি শুধু বাইরের শক্তির অনুপস্থিতি বোঝায় নাকি সেই শক্তির উপস্থিতি – যদি উপস্থিতি থাকে তবে সেই শক্তিটা কি? কোন্ কোন্ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি একটা সমাজকে স্বাধীনতার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়? স্বাধীনতা কি তবে একটা বোঝা, সেটা বহন করা মানুষের পক্ষে কি খুব বেশি ভার, যে কারণে সে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে চায়? তাহলে স্বাধীনতা কেন কারোর জন্যে একটা লালিত উদ্দেশ্য এবং অন্যদের জন্যে একটা হুমকি স্বরূপ? স্বাধীনতার সহজাত আকাঙ্খা ছাড়াও, কেন তাহলে সহজাত আনুগত্য বা বশ্যতা স্বীকারের অভিপ্রায়ও একইসঙ্গে বিদ্যমান থাকে? যদি না থেকে থাকে, তাহলে কেন আমরা নেতা-নেত্রীদের প্রতি বহু যুগ ধরে বশ্যতা স্বীকার করে আসছি? এই বশ্যতা স্বীকার কি সব সময় শুধু প্রকাশ্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় নাকি অপ্রকাশ্য কর্তৃপক্ষ যেমন কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা বা বেনামি কর্তৃপক্ষ যেমন জনমত ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়? আনুগত্যের পেছনে কি কোন লুকানো তৃপ্তি থাকে বা এর মর্ম আসলে কোথায়? কি কারণে মানুষ ক্ষমতার জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে? এটা কি তাদের কর্মশক্তির কোন শক্তিমত্তা নাকি সহজাত ও ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে জীবনকে চালিত করার দুর্বলতা এবং অক্ষমতা? এসব শক্তিমত্তা চালিত করার পেছনে মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি কি কি? কোন্ সামাজিক পরিস্থিতিতে এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলির উদ্ভব ঘটে? ধীরে ধীরে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তরে যাবো।
মানুষকে নিয়ে সব থেকে বড় সমস্যা দাঁড়ায় দুটো : এক. মানুষ একা বসবাস করতে পারেনা। অবধারিতভাবে তার সঙ্গী লাগে। এমনকি রবিনসন ক্রসোও শেষ পর্যন্ত একা থাকতে পারে নাই। ফ্রাইডে নামের একজন সঙ্গীর প্রয়োজন হয়েছিল তার। দুই. অন্য দিকে, সবার মধ্যে থেকেও মানুষ নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করে। এই নিঃসঙ্গতার প্রশ্নে ফ্রম চমৎকার একটা উদাহরণ দিয়েছেন, বালজাকের “দ্যা ইনভেন্টার্স সাফারিং” লেখা থেকে – “মানুষের ভেতর একাকিত্বের একটা ভীতি আছে। এবং সব ধরণের একাকিত্বের মধ্যে সব থেকে ভীতিপ্রদ একাকিত্ব হলো নৈতিক একাকিত্ব।” মানুষের ভেতর সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্নতা বোধ তাকে মানসিকভাবে খন্ডিত করে দেয়, ঠিক যেভাবে শারীরিক ক্ষুধা তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। শৈশব, কৈশরের একতা (মা, বাবা, ভাইবোন ও অন্যান্যদের সঙ্গে থাকা) থেকে মানুষ যত বেশি স্বাধীনতা পেতে থাকে, তত বেশি সে একজন ইন্ডিভিজুয়াল বা স্বতন্ত্র হতে থাকে। কিন্তু কাজ, ভালোবাসা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে অথবা নিরাপত্তার কারণে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকেনা । আর ঠিক সেই সময়েই তার খন্ডিকরণ শুরু হতে থাকে। ফ্রম তাই বলেছেন, মানুষ শুধু ইতিহাস দিয়ে নির্মিত হয়না, মানুষও ইতিহাস নির্মাণ করে। যে ইতিহাসের হদিস কিছুক্ষণ পরেই আমরা পাবো।
দ্বিতীয় অধ্যায়, ব্যক্তির উত্থান এং অনিশ্চিত স্বাধীনতা অধ্যায়ে ফ্রম মূলত মানুষ কিভাবে একক ব্যক্তি হয়ে ওঠে যাকে ফ্রম ‘ইন্ডিভিজুয়েশন’ বা ‘ব্যক্তিত্ব গঠন’ বলেছেন, সেসব নিয়ে আলোচনা করেছেন। শিশু ভূমিষ্ট হবার পর, নাড়ির বন্ধন ছিঁড়ে যাবার মধ্যে দিয়ে সে প্রথম স্বাধীন হয়। কিন্তু এই স্বাধীনতা শুধুই দৈহিক স্বাধীনতা, অর্থাৎ শুধু দুটো শরীরের বিচ্ছিন্নতা। একক ব্যক্তি হয়ে ওঠার (ইন্ডিভিজুয়েশন) প্রক্রিয়া শুরু হয় শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। শিশু যত বড় হতে থাকে এবং প্রাথমিক বন্ধনগুলো শিথিল হতে থাকে ততই তার ভেতর স্বাধীনতা এবং স্বাবলম্বী হবার অনুসন্ধান তীব্র হতে থাকে। কিন্তু এই অনুসন্ধানের বিষয়টা ভালো করে বুঝতে হলে ফ্রম কথিত ইন্ডিভিজুয়েশনের দ্বাদ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমের বুঝতে হবে। যে পদ্ধতির দুটো দৃষ্টিভঙ্গী আছে – এক. একদিকে শিশু ক্রমেই শারীরিক, মানসিক এবং আবেগের দিক থেকে শক্তিশালী হতে থাকে। ইন্ডিভিজুয়েশনের এই বিকাশ শিশুর নিজ শক্তিকে বাড়াতে থাকে। যদিও এই বিকাশের প্রক্রিয়া ব্যক্তির অবস্থা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক সমাজেই দেখা যায়, সমাজ ব্যক্তিকে যতটুকু জায়গা দেয় ব্যক্তির বিকাশ তার থেকে বেশি হয়না। দ্ইু. ইন্ডিভিজুয়েশনের সঙ্গে নিঃসঙ্গতার বিকাশও ঘটতে থাকে। প্রাথমিক বন্ধন (শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর) তাকে নিরাপত্তা দেয় এবং বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। কিন্তু বন্ধন মুক্তির পরেই সে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতা একদিকে তাকে শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান করে তোলে অন্যদিকে শক্তিহীন বা অক্ষম ও উদ্বেগের মুখোমুখি করে। কারণ একক ব্যক্তি যখন পৃথিবী বা বাস্তবতার মুখোমুখি হয় তখন অনেক ধরনের বিপদ-আপদ ও অতিশক্তির মুখোমুখি হতে থাকে। এই বিশাল ধাক্কা তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণের দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়েশনের প্রক্রিয়া একদিকে শিশুর বিকাশ ও নিজেকে প্রকাশ করার শক্তি যোগায় অন্যদিকে যেসব নিরাপত্তার মধ্যে সে অতীতে ছিল সেসব নিরাপত্তার বন্ধন থেকে তাকে মুক্তোও করে দেয়।
পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই মানুষের অস্তিত্ব এবং স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্য। ফ্রম দুই ধরনের স্বাধীনতার (ব্যক্তি স্বাধীনতা) কথা বলেছেন – নেগেটিভ বা ঋণাত্মক স্বাধীনতা এবং পজিটিভ বা ধনাত্মক স্বাধীনতা। তার আগে দেখা যাক, এরিক ফ্রম স্বাধীনতা বলতে কি বুঝিয়েছেন? যেসব কাজ এবং চিন্তা ব্যক্তিকে বাঁধা দিতো, সেসব বাইরের বন্ধন সে যখন মুক্ত হয়ে যায়। সে তখনই শুধু তার মনমতো কাজ করতে পারবে যখন সে জানতে এবং বুঝতে পারবে তার একান্ত চাওয়া-পাওয়াগুলিকে। অর্থাৎ বাইরের কোন প্রলোভন, ভয়ভীতি, বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তি যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার সহজাত চিন্তাগুলি করতে পারবে এবং সেই চিন্তা অনুযায়ী বিনা বাঁধায় কাজ করতে পারবে তখনই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে। এবারে আসা যাক, দুই ধরনের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে। ঋণাত্মক স্বাধীনতা হলো সেই স্বাধীনতা যা ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে, বিশ্বের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করে, অবিশ্বাসী ও বিধ্বংসী করে তোলে, আত্মাকে দুর্বল করে এবং সবসময় একটা ত্রাসের রাজ্যে বাস করে। অন্যদিকে ধনাত্মক স্বাধীনতা হলো, যেখানে ব্যক্তি একজন স্বনির্ভর ব্যক্তি হয়ে উঠে। স্বনির্ভর কিন্তু মানুষ, পৃথিবী ও প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন না। ব্যক্তি মুক্ত থাকে কিন্তু একা হয়ে বসবাস করেনা। সমালোচনামূলক কিন্তু সন্দেহমুক্ত। স্বাধীন কিন্তু মানব সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্যক্তিত্বের দুই প্রধান দিক – আবেগ এবং বুদ্ধিমত্তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজে লাগিয়ে সমন্বিত (সবার সঙ্গে একত্রে বসবাস) থাকতে পারে।
ঋণাত্মক স্বাধীনতা বোঝানোর জন্যে ফ্রম আদম-হাওয়ার মিথ থেকে উদাহরণ টেনেছেন। প্রথম যখন আদম ও হাওয়া আল্লাহর আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ফেলে সেদিন থেকেই সে আল্লহার বিরুদ্ধচারণ শুরু করে। খ্রিস্টিয় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই অমন্যতা পাপ। কিন্তু মানবজাতির দৃষ্টিকোণ থেকে এই অবাধ্যতা স্বাধীন হবার প্রথম পদক্ষেপ। কাজেই স্বাধীন হবার প্রথম সূচনা বিন্দু বাধ্যবাধকতা। এই স্বাধীনতা আরেক ধরনের পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত করে। এই স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রথম বিচ্ছেদ ঘটে। আল্লাহ তখন নারী ও পুরুষ এবং মানুষ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ করেন। যদিও মানুষ স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ সম্পন্ন করে। সে মুক্ত ও একা তবু ক্ষমতাহীন ও ভীত। তার এই নতুন স্বাধীনতা একটা পাপের মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হয়েছে ; সে মধুর স্বর্গ থেকে মুক্ত হয়েছে কিন্তু নিজেকে পরিচালিত করার ক্ষমতা তখনও অর্জন করে নাই, যে ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে তার নিজস্বতা বা স্বতন্ত্রতা অর্জন করতে পারবে। এখানে এসে ফ্রম দুটো শব্দের অবতারণা করেন – ফ্রিডাম ফ্রম এবং ফ্রিডাম টু। ফ্রিডাম ফ্রমের মাধ্যমে মানুষ স্বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিন্তু ফ্রিডাম টু এর মাধ্যমে সে এখনো স্বতন্ত্রতার দিকে যেতে পারে নাই। কারণ স্বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও, তাকে পৃথিবীর মাটি, সূর্য, চাঁদ, তারা, ফুল, প্রাণীকুল এবং মানুষের সঙ্গেই বসবাস করতে হচ্ছে। এসব বন্ধন তাকে কোন গোষ্ঠী, জাতি, সমাজ বা ধর্মের অন্তর্গত করেছে কিন্তু তার স্বতন্ত্র হবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। যদিও এসব বন্ধন তাকে এক ধরনের নিরাপত্তাও দিয়েছে। কাজেই ইন্ডিভিজুয়েশনের পথে বা ব্যক্তিত্ব গঠনের পথে একদিকে মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে শুরু করে, একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা অর্জন করে অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবোধ, অনিরাপত্তাবোধ অনুভব করে। এসব থেকে কার্যকর পরিত্রাণের উপায় হলো, নিরন্তর ভালোবাসা এবং কাজের মধ্যে দিয়ে সব মানুষের সঙ্গে কার্যকর সংহতি স্থাপন, যে সংহতি প্রাথমিক বন্ধনের মতো নয় অথচ তাকে মুক্ত ও স্বতন্ত্র মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবে। ইন্ডিভিজুয়েশনের যে পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে উল্লেখিত গোটা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করে, সেটা সব সময় মানুষকে তার স্বতন্ত্র উপলব্ধির বিষয়ে সাহায্য করেনা, বরং যে নিরাপত্তাটুকু তার ছিল সেটাও কেড়ে নেয়া হয়, তখন সেই স্বাধীনতা অসহনীয় হয়ে উঠে। এই রকম পরিস্থিতিতে শক্তিশালীরাও সেই স্বাধীনতা থেকে পালিয়ে আত্মসমর্পনের দিকে ধাবিত হয় অথবা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে হলেও মানুষের সঙ্গে এমন সম্পর্ক করে যা তাদের অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করে। মধ্যযুগের শেষ পর্বে ইউরোপ এবং আমেরিকার ইতিহাস ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের উত্থান পর্বের ইতিহাস। যা শুরু হয়েছিল ইতালির রেনেসাঁ পর্ব থেকে এবং বর্তমানে যার চুড়ান্ত অবস্থা চলছে। মধ্যযুগীয় বিভিন্ন বাঁধাবিপত্তি ও সংযমের শৃঙ্খলা ভাঙতে ইউরোপের প্রায় চারশ বছর সময় লেগেছিল। এরমধ্যে স্বাধিনতা থেকে (ফ্রিডম ফ্রম) স্বাধীনতার দিকে (ফ্রিডম টু) ধাবিত হবার ফাঁক বিশাল আকার নিয়ে নিয়েছে। রিফরমেশনের মধ্যে দিয়ে নতুন ধরনের স্বাধীনতার সংজ্ঞা এসে হাজির হয়। আধুনিক গণতন্ত্রের স্বাধীনতার সংজ্ঞা এই রিফরমেশনের বীজের মধ্যে নিহিত। এবার সেই স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করা হবে।
তৃতীয় অধ্যায়ে রেনেসাঁ ও রিফরমেশনের সময়ে স্বাধীনতার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ ইতিহাস ভিত্তিক। অর্থাৎ মধ্যযুগ নিয়ে আলোচনার পর রেনেসাঁ ও রিফরমেশনের মধ্যে দিয়ে কিভাবে ব্যক্তি স্বাধীন হতে শুরু করে এবং এসব স্বাধীনতা তাকে কি দিয়েছে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা। ফ্রম এখানে বলছেন, ইউরোপীয় মধ্যযুগকে দুইভাবে বিকৃত করে দেখা হয় – এক. আধুনিক যুক্তিবাদীরা মধ্যযুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেন। দুই. প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিকেরা মধ্যযুগকে অতি মাত্রায় আদর্শায়িত করেছেন। আসলে মধ্যযুগকে দেখতে হলে, দুটোকে মিলিয়ে দেখতে হবে। ফ্রম এখানে মধ্যযুগের কিছু বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন, মধ্যযুগে শ্রেণি বৈষম্যের কড়াকড়ির কারণে এক শ্রেণি অন্য শ্রেণির সঙ্গে মিশতে পারতনা, দেশান্তর খুব কম হতো, মধ্যযগীয় শহরের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠগুলি তুলনামূলকভাবে স্থবির ছিল, এই যুগের কর্মাস মূলত ছোট ছোট ব্যবসায়ী দিয়ে গঠিত ছিল, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা তখনও আলাদা হয় নাই, লোভকে পাপের সমতুল্য মনে করা হতো, সামাজিক নিয়মই প্রচলিত নিয়ম ছিল, নিরাপত্তার দায়িত্ব সমাজের উপর ছিল, সীমাবদ্ধতার মধ্যেও মানুষের কথা বলার, আবেগ প্রকাশ করার অধিকার ছিল, দুঃখদুর্দশাও ছিল, কিন্তু সেসব দুর্দশা দূর করার জন্যে গির্জা ছিল, সামাজিক বন্ধন দৃঢ় ছিল, ব্যক্তি স্বাধীনতায় বাঁধা ছিলনা, কারণ ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা তখন জন্মায়ই নাই, পুঁজির আগমনের সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা দাঁনা বাঁধতে শুরু করে ইত্যাদি। আধুনিক ইতালির ইউরোপের রেনেসাঁ হলো প্রথম সন্তান যে স্বতন্ত্রবাদ বা ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে আসে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই বার্গার বা নগরবাসী এবং এলিট বা সমভ্রান্তরা দেয়াল ঘেরা শহরে একসঙ্গে বসবাস শুরু করে। বংশ মর্যাদার জায়গা দখল করে আর্থিক মর্যাদা।
রেনেসাঁ সংস্কৃতি ছিল মূলত ধনী ও শক্তিশালী উঁচু শ্রেণীর সংস্কৃতি। ছোট ব্যবসায়ী বা পেটি বুর্জোয়াদের না। রেনেসাঁ সংস্কৃতি এই উঁচু শ্রেণীকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অনুভূতি এনে দিলো। কিন্তু একইসঙ্গে মধ্যযুগীয় নিরাপত্তা থেকে তারা বঞ্চিত হলো, ফলে স্বাধীন হয়েও তার নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। এসব স্বতন্ত্র ব্যক্তির দল অহংবোধে ডুবে থাকতো। শিল্প-কারখানা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির বিস্তার ঘটতে থাকে। টাইম ইজ মানি ধারণার জন্ম হতে থাকে। মধ্যযুগের শেষের দিকে, রেনেসাঁর শুরুতে এক ধরনের অস্থিরতা শুরু হতে থাকে। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা উদ্ভবের ফলে নতুন এক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটতে থাকে। বাজারে পুঁজির বিকাশ ও প্রতিযোগিতার ফলে ব্যক্তি মানুষকে ক্রমেই অনিশ্চয়তা, বিচ্ছিন্নতা এবং উদ্বেগের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। যে পুঁজি আগে মানুষের দাস ছিল সে-ই এখন মনিব হয়ে উঠে। একেকটা বাজারের দিন, শেষ বিচারের দিক হয়ে দাঁড়ায়। সামন্ত্রতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সহযোগিতামূলক, প্রতিযোগিতা সেখানে বাঁধাপ্রাপ্ত হতো। নতুন পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেল যে, হয় ব্যক্তিকে সাঁতার কাটতে হবে অথবা ডুবে মরে যেতে হবে। নতুন এই স্বাধীনতা মানুষকে ব্যক্তি-শূন্যতা ও অসহায়ত্বের অনুভূতিতে বিধ্বস্ত করে দিলে। জঁ পল সাত্রের দর্শন অনুযায়ী, স্বার্গের উদ্যান সে হারিয়েছে ভালোর জন্যে, ব্যক্তি এখন একা পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে – কেউ তাকে অনন্ত হুমকির পৃথিবীতে ছুঁড়ে দিয়েছে। এই নব্য স্বাধীনতা ব্যক্তি-মানুষকে নিরাপত্তাহীনতা, শক্তিহীনতা, সন্দেহ, নিঃসঙ্গতা এবং উদ্বেগের গভীর অনুভূতির জালে জড়িয়ে ফেলে। ঠিক এই সময়েই লুথারবাদ এবং ক্যালভিনবাদের আগমন ঘটে।
রেনেসাঁ ও রিফরমেশন আন্দোলনের মধ্যে মূল যে পার্থক্য ছিল সেটা হলো – রেনেসাাঁর (১৪০০) সময়ে শিল্প ও বাণিজ্য পুঁজির বিশাল প্রসার ঘটেছিল। গুটিকয়েক ধনী শক্তিশালী শ্রেণীর দ্বারা সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এবং দার্শনিক ও শিল্পীরা এই ধনী শ্রেণী দ্বারা উদ্দীপিত হচ্ছিল। আর্থিক নিশ্চয়তা এই ধনী শ্রেণীকে নতুন এক ধরনের নিশ্চয়তা ও স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। একইসঙ্গে নিরাপত্তাহী, শক্তিহীন (পুঁজির উপর আত্মসমর্পন ), নিঃসঙ্গও করে তুলছিল। অন্যদিকে রিফরমেশন (১৫১৭) ছিল ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। শহরের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও কৃষদের আন্দোলন, যা লুথার ও ক্যালভিনের হাত ধরে এসেছিল। এই আন্দোলনের ফলে প্রটেস্টট্যান্টবাদ ও ক্যালভিনবাদ গড়ে উঠে। লুথার ও ক্যালভিনের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের আলোচনার সময়ে, ফ্রম গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য দেন। যখন কোন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতবাদ মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যের জায়গা থেকে আলোচনা করা হয়, তখন দুটো সমস্যার দিকে খেয়াল রাখতে হয। এক. যিনি কোন নির্দিষ্ট মতবাদ প্রচার করেন, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা, কোন্ বৈশিষ্টের কারণে তিনি এই মতবাদ প্রচার করেছেন। দুই. সেই নির্দিষ্ট সমাজের চরিত্র, যে চরিত্রের কারণে কোন নির্দিষ্ট সমাজে, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির মতবাদ গ্রহণ করে। ফ্রম লুথার এবং ক্যালভিনের চরিত্র বর্ণনা করে দেখেন, দুজনই অন্যান্য কারণের সঙ্গে চার্চের বাধ্যবাধকতাকে (বিশেষ করে পোপের কর্তৃত্ত্ব) ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করেন। ফলে চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মমত প্রচার শুরু করেন। উল্লেখ্য, লুথার এবং ক্যালভিন দুজনেই যেহেতু খ্রিস্টিয় ধর্মমতে বিশ্বাসী, তাই তাদের বিশ্বাস সেইভাবে পরিচালিত হয়েছে। লুথার (জার্মানি) এবং ক্যাভিনের (অ্যাঙ্গলো সেক্সান) মতবাদে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায়না। দুজনেই পরিপূর্ণ সমর্পণ তাদের গডের বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিয়েছে। একমাত্র এই বিশ্বাসের জোরেই মানুষ নিষ্কৃতি বা মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু এই জোরজবরদস্তিমূলক নিশ্চয়তার প্রতি আহবান কোন অকৃত্রিম বিশ্বাস থেকে নয় যতটা সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটা উপায়ের কারণে করা হয়েছে (যে সন্দেহ নিয়ে আধুনিক মানুষের দর্শন শুরু হয়েছে )। লুথার মানুষের ভেতরে থাকা অসাধুতা, পচলশীলতা দুর করার উপর জোর দিয়েছেন, ক্যালভিন ধর্মের শেকড় খুঁজেছেন মানুষের শক্তিহীনতা, আত্ম-অপমান, নিজেদের তুচ্ছ করে ভাবা, ও অহংকার চূর্ণ করার মধ্যে। দুজনের ধর্মীয় সংস্কার বিবেচনা করলে দেখা যায়, মধ্যযুগের গির্জার সঙ্গে লুথাববাদ, ক্যালভিনবাদ, প্রটেস্টট্যান্টবাদের সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। গির্জা যেমন কর্তৃত্ববাদের কথা বলে, এই দুই মতবাদেও দেখা যায়, গির্জা না থাকলেও গড নামক আরও উচ্চতর কর্তৃত্বের কথা বলা হয়। এখানে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে খ্রিস্টিয় ধর্মের পার্থক্য আমরা খেয়াল করতে পারি। খ্রিস্টিয় ধর্মে গডকে যেমন প্রভু অর্থাৎ কর্তৃত্বের জায়গায় স্থান করে দেয়া হয়েছে, ইসলাম ধর্মে আল্লার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রভু নয়, বন্ধুর মতো। বন্ধুত্বে কোন কর্তৃত্ব থাকেনা। এটা ভিন্ন তর্ক। এবার আমরা ফ্রমের চতুর্থ অধ্যায় এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় অধ্যায়, ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রে আধুনিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কি বলেছেন দেখবো।
আধুনিক মানুষের ঋণাত্মক স্বাধীনতার বোঝা বুঝে ওঠা এতো সহজ কাজ না। কারণ আধুনিক মানুষ তার স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে পুরানো কর্তৃত্বের বাঁধাগুলি দূর করতে যেয়ে দেখলো, নতুন নতুন কর্তৃত্ব ও বাঁধা এসে হাজির হয়েছে। পুরানো শত্রুর জায়গায় নতুন শক্র এসে হাজির হয়েছে, যে শত্রু তার স্বাধীন হবার পথে বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকেই দরজা বন্ধ করে দেয়, যা আরও ভয়াবহ। যেমন, মানুষ এক সময় বিশ্বাস করতো, তার ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে গির্জাই একমাত্র বাঁধা। কারণ গির্জা মানুষের বিবেকের ভালো-মন্দ বিচারের কর্তা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আধুনিক সময়ের মানুষ সবকিছুর উপর এমনভাবে বিশ্বাস হারাতে শুরু করলো যে, যে অবিশ্বাস প্রাকৃতিক, কোন বৈজ্ঞানিক কৌশল দিয়ে নির্ণয় করা যায়না। আধুনিক যুগে ‘বাক স্বাধীনতা’ কে ব্যক্তি স্বাধীনতার সর্বোচ্চ মানদন্ড হিসাবে দেখা হলো। মানুষ এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল, যেখানে সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ও কথা বলতে পারে। কিন্তু এটা করতে যেয়ে সে ভেবে দেখলনা যে, সে যা চিন্তা করে এবং বলে, সেটা তার একার দখলে নেই, যে দখলের মধ্যে অন্য কেউ তার চিন্তা বা মতের বিরুদ্ধচারণ করতে পারবেনা। যা একান্তই তার নিজস্ব মৌলিক চিন্তা। মানুষ উচিৎ-অনুচিতের কর্তৃত্বপরায়নতা থেকে মুক্ত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু যেটা সে উপেক্ষা করেছে সেই বেনামা কর্তৃত্ব যেমন, জনমত এবং কান্ডজ্ঞান (কমনসেন্স) – যা খুবই শক্তিশালী, কারণ এসব জনমত মেনে নেয়া আর না-নেয়া আমাদের উপরেই নির্ভর করে। অর্থাৎ আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতার বিজয় বাইরে থেকে দেখে যতই মুগ্ধ হইনা কেন, আমাদের ভেতরের সংযম, বাধ্যবধকতা এবং ভয়ের প্রতি একটা অন্ধ বিশ্বাস থেকেই গেল। আধুনিক মানুষ, ‘মানুষ’ কে তার সব কাজের কেন্দ্রে নিয়ে আসলো। অর্থাৎ সে যা করে নিজের জন্যে করে ; নিজ স্বার্থ এবং অহংবোধ সব কাজের শক্তিশালী প্রেরণা হয়ে হাজির হলো। ঠিক যেভাবে লুথার এবং ক্যালভিন মানুষকে তুচছজ্ঞান করেছিল, মুক্তির উপায় হিসাবে গড বা আল্লাহর কাছে সমর্পণের দিকে দিক নির্দেশনা দিয়েছিল, আধুনিক সমাজে ঠিক একইভাবে মুনাফার লোভ দেখিয়ে মানুষকে পুঁজির সঙ্গে বেঁধে দেয়া হলো, যে মুনাফার আশায় মানুষ কাজ করে। সেই মুনাফা আবার পুঁজির কাজের জন্যে বিনিয়োগে চলে যায়, বর্ধিত মুনাফা আবার বর্ধিত পুঁজি বিনিয়োগে চলে এবং এভাবে চক্রহারে ঘুরতে থাকে।

যেকোন সমাজে সংস্কৃতির আত্মা সেই সমাজের শক্তিশালী শ্রেণীবর্গ দ্বারা নির্ধারিত হয়। কারণ শিক্ষা ব্যবস্থা, বিদ্যালয়, গির্জা, তথ্যপ্রবাহ, নাটক-সিনেমা ইত্যাদি এই শ্রেণীর চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তারা এমন প্রতাপশালী হয় যে নিম্ন শ্রেণী ও সাধারণ জনগণ এই শক্তিশালী শ্রেণীকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেয় এবং মানসিক ভাবে তাদের পথ অনুসরণ করে। আধুনিক মানুষের কাছে প্রেরণা আসে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে বা সাধনার মাধ্যমে নয়, প্রেরণা আসে চুড়ান্ত অহংবোধ এবং নিজস্বার্থ সাধনার মধ্যে দিয়ে। আধুনিক মানুষ স্বার্থপর। স্বার্থপর অর্থাৎ লোভী। কিন্তু এই লোভের শিকড় থাকে নিজ স্বার্থের হতাশার মধ্যে, যার লক্ষ্যবস্তু সমাজ, যেখানে গ্রথিত বা বোনা আছে। কারণ আধুনিক মানুষ দেখলো, উৎপাদন প্রক্রিয়ার আসল মালিক সে নয়, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি। ফলে তার ত্যাগ জড়িয়ে পড়লো অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব, যুদ্ধ, আগ্রাসন ইত্যাদির সঙ্গে। সে তার নিজের তৈরি পণ্য থেকে ছিটকে পড়লো। যে প্রকৃতিকে সে বধ করতে চেয়েছিল সেই প্রকৃতিই এখন তাকে বধ করছে। নিজের তৈরি কাজ তার সামনে আল্লাহ্ হয়ে হাজির হলো। নিজেকে মানুষ পৃথিবীর কেন্দ্রে আছে বলে বিভ্রমে ভোগে অন্যদিকে তুচ্ছতা ও শক্তিহীনতা তাকে ঘিরে রাখে, ঠিক যেভাবে তার পূর্বসুরীদের খোদার দোহাই দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সব সম্পর্কের মধ্যে বাজারের নিয়মই আসল নিয়ম। পণ্য বিক্রি করতে করতে একসময় সে নিজেকেও বিক্রি করে দেয়। একজন শ্রমিক তার শারীরিক শ্রম বিক্রি করে, কিন্তু ব্যবসায়ী, ডাক্তার, চাকরিজীবী প্রমুখেরা নিজের ব্যক্তিত্বকেই বিক্রি করে দেয়। এমনকি একজন ক্রেতা যখন দোকানে কিছু কিনতে যায় ভোক্তা হিসাবে সে মূল্য পায়। কারণ এই মূল্য না পেলে, বিক্রেতা একজন ভোক্তাকে হারাবে এবং তার ক্ষতি হবে। অর্থাৎ বিমূর্ত ভোক্তা হিসাবে ভোক্তার মূল্য আছে কিন্তু মূর্ত ভোক্তা হিসাবে তার কোন মূল্য নেই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একই চিত্র দেখা যায়। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভোটাদের মূল্য শুধু ভোটের সময়। নির্বাচন শেষ ভোটারের মূল্যও শেষ। এভাবেই আধুনিক মানুষ ক্রমেই বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হতে থাকে।
মানুষের এসব বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা, বিশেষ করে ফ্যাসিস্ট এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেখা যায় এবং পরিণতিতে মানুষ ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে, যা মেকানিজমস অফ স্কেপ বা পালানোর কৌশল নামে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূল আলোচনার আগে সমাজে বসবাস করা দুই ধরনের মানুষের কথা ফ্রম বলেছেন – স্বাভাবিক বা সুস্থ মানুষ এবং নিউরোটিক মানুষ। স্বাভাবিক বা সুস্থ মানুষ তারাই, যারা সমাজ কর্তৃক আরোপিত কাজগুলি করতে পারে অর্থাৎ সমাজের হাওয়া বা ফ্যাশন অনুযায়ী চলতে পারে। সমাজের কাজ মসৃণভাবে সম্পন্ন করার জন্যে এবং নিজের ব্যক্তিত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে গঠন করার দিক থেকে এদের মধ্যেও আবার ভিন্নতা থাকে – প্রথম দল সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী চলে এবং শেষোক্ত দল নিজের আদর্শ ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। এসব বিষয় মনোবিজ্ঞানীরা প্রায়ই উপেক্ষা করে থাকেন। অন্যদিকে নিউরোটিক মানুষ খুব সহজে নিজেকে বিসর্জন দিতে রাজি থাকেনা। যদি সে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র রক্ষায় ব্যর্থও হয়, সে তখন নিজের সক্রিয়তা প্রকাশের চেয়ে নিউরোটিক সিমটম এবং ফ্যান্টাসি থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজেকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। ফ্রমের মতে, মানবিক মূল্যবোধের দিক থেকে নিউরোটিক মানুষের চেয়ে সুস্থ মানুষ বেশি পঙ্গু হয়ে থাকে। হতে পারে সুস্থ মানুষ নিজের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে তাকে যেভাবে সমাজ আশা করে সেভাবে সে নিজেকে প্রকাশ করে, কিন্তু তার সহজাত স্বাতন্ত্রবোধ এবং স্বাধীন ইচ্ছাগুলিকে বিসর্জন দিতে হয়। স্বাধীনতা থেকে পলায়নের ক্ষেত্রে এই দুুই ধরণের চরিত্র প্রায় একইরকম হয়ে থাকে।এখন আমরা ফ্যাসিস্ট এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তি কেন ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে পালাতে চায় দেখবো।
ফ্যাস্টিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা মূলত ধর্ষকামী (স্যাডিসস্টিক) মনস্তাত্তিক চরিত্র থেকে উৎপন্ন হয়। তিন ধরনের ধর্ষকামী প্রবণতা দেখা যায় – এক. এক ধরনের ধর্ষকামী চরিত্র আছে যারা অন্যদের তার নিজের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। দুই. আরেক ধরনের ধর্ষকামী অন্যদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আরোপ করে। জনগণকে নাচের পুতুলে পরিণত করে। তিন. আরেক ধরন, জনগণকে ক্রমাগত শোষণ করে। এই ধরনের ধর্ষকামীরা অন্যদের নিরন্তর ভোগান্তিতে রাখে। ধর্ষকামীরা মর্ষকামীদের (ম্যাসোকিস্টিক) থেকে তুলনামূলকভাবে কম সচেতন হয় এবং তারা নিজেদের কাজকে যৌক্তিক করে তোলে। যেমন কোন ধর্ষকামী নেতা বা নেত্রী এই মনোভাব পোষণ করতে পারে যে, যেহেতু আমি জাতির কাছ থেকে প্রচন্ড আঘাত পেয়েছি, কাজেই জাতির উপর প্রতিশোধ শুধু আমিই নিতে পারি। আরেক ধরনের ধর্ষকামী আছে, যে শুধু তাকেই ভালোবাসে যার উপর সে প্রভুত্ব করতে পারে। ঘুষ দিয়ে অপরকে বশে রাখে। এমনকি সে সব দিয়ে দিতে প্রস্তুত শুধু স্বাধীনতা ছাড়া। অর্থাৎ পরাধীন করে রাখা। মর্ষকামী বিকৃতি অন্যদিকে ধারণা করা হয়, অপরের দ্বারা শারীরিক চরম ব্যথা পাওয়ার মধ্যে দিয়ে এক ধরনের যৌন সুখ অনুভব করে। কিন্তু এটাই একমাত্র মর্ষকামীতা না। নৈতিকভাবে অপরকে দুর্বল করে দেয়ার মধ্যে দিয়ে মর্ষকামী এক ধরনের আনন্দ অনুভব করে। অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার মধ্যে দিয়ে মর্ষকামী সুখ পায়। ফ্রয়েডের মতে মর্ষকামী হয় নিজেকে ধ্বংস করে নয় অপরকে। এদের কারণে অর্থাৎ ধর্ষকাম এবং মর্ষকাম চরিত্রের কারণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার লয় ঘটে। চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিদের শিকড় শক্তিশালী হয়না। দুর্বল চরিত্রের মানুষেরাই ক্ষমতালিপ্সু হয়ে থাকে। আত্মনির্ভলশীল হয়ে যারা দাঁড়াতে পারেনা, তারাই ক্ষমতার কাঙাল হয়। যেহেতু তাদের ভেতরে অকৃত্রিম বা খাঁটি শক্তি নেই, তাই তারা ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় রাস্তা খোঁজে। ক্ষমতার দুই রূপ – এক. অন্যকে দমিয়ে রাখা এবং দখলে রাখার জন্যে ক্ষমতা। দুই. নিজেকে ক্ষমতাশালী দেখানোর ক্ষমতা। আধিপত্য প্রয়োগের জন্যে যে ক্ষমতা সেটা বিকৃত ক্ষমতা। আধুনিক সময়ে প্রকাশ্য কর্তৃত্বের চেয়ে অপ্রকাশ্য কর্তৃত্ব যেমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও, কর্তব্য, বিবেকিতা, অতিঅহং ইত্যাদি দ্বারা মানুষ শোষিত হয় বেশি। যেটা মানুষ বুঝতে পারেনা অথচ প্ররোচিত হতে থাকে। যেখানে কর্তৃত্ববাদী চরিত্র থাকে, সেখানে ক্ষমতাশীল এবংং ক্ষমতাহীন – এই দুই দলে বিভক্ত থাকে। কর্তৃত্ববাদী চরিত্র বিপ্লবী হয়না, বরং সন্ত্রাসী চরিত্রের হয়। মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে। মানুষের ভালোবাসা পাবার চেয়ে ঘৃণিত হতে বেশি পছন্দ করে। কর্তৃত্ববাদী চরিত্র অতীতে বিচরণ করে। কিন্তু জীবন এগিয়ে যায়, প্রকাশিত হতে চায় এবং স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে চায়। যখন এসব ক্ষেত্রে বাঁধা আসে তখন মানুষ স্বাধীনতা থেকে পলায়নের কৌশল হিসাবে ধ্বংসাত্মক কাজ বেছে নেয়। ধ্বংসাত্মক জীবন যাপিত জীবন না করার বহিঃপ্রকাশ। আরেকটা কৌশল সে বেছে নেয়, ফ্রমের ভাষায় অটোমেটন যার বাংলা অনুবাদ কঠিন হলেও, স্বয়ংক্রিতা হিসাবে এখানে করা হলো। ব্যক্তি তখন সমাজের চাহিদা অনুযায়ী চলার পথ বেছে নেয়। ফলে তার নিজের অনেককিছু বিসর্জন দিতে হয়। অনেকটা এক গোয়ালের গরু হয়ে বেঁচে থাকা। ফলে সে নিঃসঙ্গ ও উদ্বেগ অনুভব করেনা। কিন্তু এইজন্যে যে ক্ষতিটা হয় সেটা হলো, সমাজ থেকে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মতামত, স্বাধীন কাজ দূর হয়ে যায়। মিথ্যা চিন্তা প্রকৃত চিন্তাকে ঢেকে দেয়, যে চিন্তার নাম ফ্রম দিয়েছেন স্যুডো থিংকিং। যেমন কাউকে যদি রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাহলে সে দৈনিক পত্রিকা, টিভির খবর ইত্যাদি পড়ে বা শুনে সে যা দেখেছে শুধু সেটা বলে যাবে। একই ঘটনা নান্দনিক ক্ষেত্রেও ঘটে। কোন চিত্র প্রদর্শনীতে উদাহরণস্বরূপ, রেমব্রার চিত্রকর্ম থাকলে দর্শক সেই ছবিকে বাহাবা দিবে। এমন না, যে রেমব্রার আঁকা তার খুব পছন্দ, যেহেতু রেমব্রা বিখ্যাত, সবাই তার ছবির প্রশংসা করে, তাই তাকেও করতে হবে। এভাবে পত্রিকা পড়ে বা টিভি দেখে বা লোকমুখে শুনে শুনে একসময় মানুষের কাছে ঘটনাগুলি সত্য বলে মনে হয়। চিন্তার এই দমনের কাজ শিশুকাল থেকেই গড়ে তোলা হয়। লেখা দীর্ঘ হবার কারণে উল্লেখ করা হলোনা। ভুল চিন্তা বা স্যুডো থিংকিং-এর সমস্যাটা হলো, চিন্তাটা সঠিক নাকি বেঠিক সেটা নয়, চিন্তাটা তার নিজের প্রসুত কিনা। কি চিন্তা করা হয় তারচেয়ে প্রধান বিচার্য “কিভাবে চিন্তা করা হয়”। নিজস্ব চিন্তা নতুন হয়। এভাবে দেখা যায়, আমাদের অনেক সিদ্ধান্ত আমাদের নয়, বাইরে থেকে আসা কোন পরামর্শ। অথচ আমরা সার্থকভাবে নিজেদের প্ররোচিত করি যে সিদ্ধান্তগুলি আমাদের। প্রকৃতপক্ষে যেটা হয় সেটা হলো – অন্যের প্রত্যাশা পূরণের জন্যে বা বিচ্ছিন্নতার ভয় বা স্বস্তি বা আরামের প্রতি হুমকির ভয় থেকে আমরা এসব করে থাকি। মানুষ এভাবে অন্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে করতে এক সময় নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং তার ভেতর সৃষ্টি হয় এক কৃত্রিম ‘আমি ’। যে আমি তাকে সব সময় একটা অনিরাপত্তাবোধের মধ্যে রাখে। সে সন্দেহ দ্বারা অন্ধকারাবৃত থাকে। অন্য মানুষের প্রত্যাশা প্রতিফলিত হতে থাকে তার উপর। ‘আমি’ কে হারানোর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে তখন বাধ্য হয়, অন্যের অনুমোদন এবং স্বীকৃতি পাবার জন্যে, অনবরত নিজেকে অন্যের উপযোগী করে গড়ে তুলতে থাক। এভাবে ‘স্যুডো থিংকিং বা চিন্তা ‘স্যুডো সেল্ফ বা আত্মো ’, ‘স্যুডো উইশ বা ইচ্ছা’ মানুষকে শেষ পর্যন্ত একটা যন্ত্রে পরিণত করে, যে যন্ত্রের ব্যবহার করে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র টিকে থাকে।
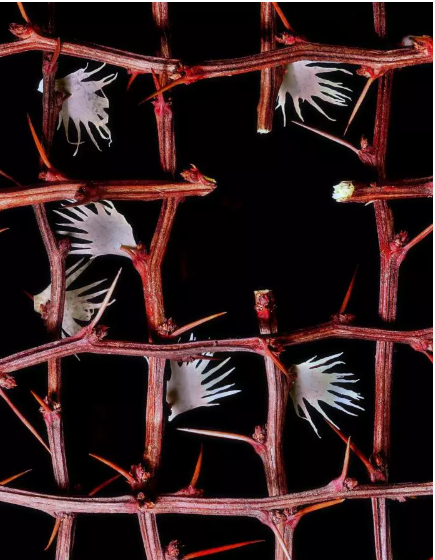
ষষ্ঠ অধ্যায় নাৎসিবাদের মনস্তাত্তিক ও অন্যান্য দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নাৎসিবাদ কিভাবে এবং কোন্ কৌশলে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করেছিল, এই অধ্যায়ে আমরা দেখি। মামফোর্ড তার ফেইথ ফর লিভিং বইয়ে জানিয়েছেন, নাৎসিবাদ ফ্যাসিজমের মতো অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কোন বিষয় না। এটা সম্পূর্ণ মনস্তাত্তিক বিষয়। ফ্রম এই মতকে নাকচ করেন। তার মতে নাৎসিবাদের উদ্ভবের পেছনে, অর্থনৈতিক গতিশীলতা – জার্মান সা¤্রাজ্যবাদ বিস্তারের তীব্র প্রবণতা এবং শিল্পপতি ও তরুণ জার্মান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সংখ্যালঘুর চালাকী এবং সংখ্যাগুরুর উপর দমনপীড়কে মনে করেন। হিটলার এই শিল্পপতিদের হাত ধরেই ক্ষমতায় এসেছিলেন। নাৎসিবাদ সার্থক হবার পেছনে দুটো মূল কারণ ধরা হয় – এক. জনগণের এক অংশ (শ্রমিক শ্রেণী) নাৎসিবাদকে বিনা বাঁধায় মেনে নিয়েছিল। দুই. অপর অংশ (লিবারেল ও ক্যাথলিক বুর্জোয়া) এই মতাদর্শের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়েছিল। নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত শ্রমিক শ্রেণী মনস্তাত্তিকভাবে তাদের দুর্দশা দ্রুত দূর করার জন্যে নাৎসি সময় থেকে বর্তমান গণতান্ত্রিক সময় পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে ক্লান্তিকর আত্মসমর্পনের মধ্যে দিয়ে গেছে, কিন্তু ফ্রম সংজ্ঞায়িত স্বাধীনতার সাধ এখনো অধরাই থেকে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্যবিত্ত বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত একচেটিয়া পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার হুমকির সম্মুখীন হয়। তাদের ভেতর ঘৃণা ও উদ্বেগ বাড়তে থাকে; তারা এক আতঙ্কের পর্যায়ের চলে যায় এবং আত্মসমর্পন এবং শক্তিহীনের উপর দমনের লোভ বাড়তে থাকে। এই মধ্যবিত্তের ত্রানদাতা হিসাবে হিটলার তখন হাজির হলেন। হিটলারের ধর্ষকামী চরিত্র নিয়েও এখানে আলোচনা হয়েছে। যেহেতু আগেই আমরা এই চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাই এই অধ্যায় নিয়ে আর বেশিকিছু আলোচনা করার নেই।
সপ্তম এবং শেষ অধ্যায় – স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রে এরিক ফ্রম আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ কতটুকু ব্যক্তিস্বতন্ত্র বা ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে বা আদৌ অর্জন করতে পেরেছে কিনা সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কর্তৃত্ববাদের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা তখনই সম্ভব হয় যখন আমাদের অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্তিক অবস্থা এমন হয় যে আমরা আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই। প্রশ্ন হলো সেটা অর্জন সম্ভব কিনা? মূলত এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই ফ্রমের বইটি লেখা। এর উত্তর খোঁজার জন্যে ফ্রম দুটো দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টা বিবেচনা করেছেন – এক. অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন, যে অর্থনৈতিক অবস্থা মানুষকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন করে তোলে। দুই. মনস্তাত্তিক দৃষ্টিকোন, যে দৃষ্টিভঙ্গীর ফলাফলে আমরা দেখেছি এই শক্তিহীনতা কর্তৃত্ববাদের ক্ষেত্রে মানুষকে পলায়নপর করে তোলে অথবা তার বিচ্ছিন্নতা তাকে যন্ত্রমানব বা রোবটে পরিণত করে। নিজেকে সে হারিয়ে ফেলে। অথচ সে মনে করে সে মুক্ত, স্বাধীন। সে শুধু তারই বিষয় অন্য কোনকিছুর বিষয় না। এই কারণে ফ্রম, দুই ধরনের স্বাধীনতার কথা বলেছেন – ঋনাত্বক এবং ধনাত্বক স্বাধীনতা, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফ্রম দেখিয়েছেন, গণতন্ত্রের এই যুগেও, মানুষকে কি করে মেনে চলার সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করা হয়, আমাদের আবেগ-অনুভূতিগুলিকে দমিয়ে রাখা হয়, যার শুরু শিশুকাল থেকেই শুরু হয়। ফ্রম তাই মেকি স্বাধীনতা অর্থাৎ ঋনাত্মক স্বাধীনতা থেকে ধনাত্মক স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যেতে বলেন। যে স্বাধীনতা মানুষকে শুধু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এনে দিবেনা, সেই সঙ্গে মানুষকে সহজাত, স্বতঃস্ফূর্ততা আনার পাশাপাশি তাকে কখনো বিচ্ছিন্ন করে তুলবেনা, করবেনা শক্তিহীন। শুধু তখনই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে।
- ফ্লোরা সরকার : অভিনেত্রী, লেখক, শিক্ষক
- প্রথম প্রকাশ: ৫ম বর্ষ-৩য় সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২), ত্রৈমাসিক দেশকাল পত্রিকা