
- মোহাম্মদ আজম
শিরোনামে ‘সময়’ কথাটার কানে উদ্ধৃতি-চিহ্ন জুড়ে দিয়ে এবং শিরোনামের শব্দবন্ধে ‘সময়’ শব্দটাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার মধ্য দিয়ে আমরা এখানে রবীন্দ্র-সাহিত্যের, আমাদের বিবেচনায়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবসম্পদের আলোচনায় আসলে তাঁর কালকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছি। এই অনুমান থেকে যে, সময়ের আনুকূল্যই আদতে ব্যক্তি মানুষের কৃতি ও কৃতিত্বের প্রধান অনুপান। ব্যক্তির প্রস্তুতি ও শ্রম, মেধা ও সৃষ্টিশীলতা মোটেই গৌণ ব্যাপার নয়। কিন্তু ইতিহাসে এ ধরনের মেধাবী ও সৃষ্টিশীল সমস্ত মানুষের আবির্ভাবের সময়গুলো পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, বড় কাজের যাবতীয় বাস্তবতা ও বড় সংকট তথা প্রশ্ন নিয়ে সময়গুলো অপেক্ষা করছিল বড় প্রতিভার জন্য। অর্থাৎ, সময়ের সংকট ও প্রশ্নই আসলে বড় প্রতিভার জন্ম দেয়, আর অনুকূল প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে তাঁরা বড় কাজগুলো সম্পন্ন করেন।
তো, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সময়টি কেমন ছিল?
প্রথমে সাহিত্যিক সময়ের কথা বলা যাক। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সময়কে বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে প্রথম বড় ধরনের ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কিন্তু সে ঝাঁকুনি সম্পূর্ণ অচেনা ছিল না; বড় ধরনের বিপর্যয় তাতে ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সময় প্রায় সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল কল্লোলীয়দের হাতে। তার নন্দনতাত্ত্বিক তাৎপর্য আমাদের এখনকার আলাপের জন্য জরুরি নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে ওই নতুন নন্দনদৃষ্টি কী ভীষণ অচেনা ছিল, তার পরিচয় রবীন্দ্র-সাহিত্যেই এন্তার পাওয়া যায়। আমি এখানে নমুনা হিসাবে কেবল ‘সাহিত্যের স্বরূপ’ বইয়ের নাম-প্রবন্ধের উল্লেখ করছি। এ প্রবন্ধে পরিষ্কার বোঝা যায়, নতুন প্রজন্মের ছাঁচাছোলা বাস্তবতায় রবীন্দ্রনাথ শুধু বিরক্তই ছিলেন না, তিনি আসলে ওই বাস্তববাদিতা কোনো অর্থেই আমলে আনতে পারেন নাই। যে অর্থে সুধীন্দ্রনাথ দত্তরা নিজেদের ‘বিংশ শতাব্দী’র সমান বয়সী বলে ঘোষণা করতেন, সে অর্থে রবীন্দ্রনাথ মোটেই বিশ শতকের নন, যদিও তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের বড় অংশ এবং হয়ত সফল অংশ বিশ শতকেই কেটেছে। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমা অর্থে এবং ভারতীয় অর্থে বিশুদ্ধ উনিশ শতকের লেখক।

কিন্তু কেমন ছিল এ উনিশ শতক?
সাহিত্যিক অর্থে বাংলা সাহিত্যের উনিশ শতকের চিহ্নায়ক সাহিত্যিকগণ হলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু সামাজিক-রাজনৈতিক তথা ভাবগত অর্থে বাংলার উনিশ শতকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর ঔপনিবেশিক শাসন। এ শাসনের সাথে তাল রেখে বিকশিত হচ্ছিল পশ্চিমায়িত নাগরিক শিক্ষিত শ্রেণি; সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তরে ঘটছিল পশ্চিমায়ন ও আধুনিকায়ন। আজকাল ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ বিষয়ে মতানৈক্য খুব কম যে, উনিশ শতকের গোড়া থেকে ব্রিটিশ লিবারেল চিন্তাভাবনার নানা বৈশিষ্ট্য কলকাতার শিক্ষিত সমাজের অগ্রসর অংশে রাজত্ব করছিল। রামমোহন রায় ও তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এ ভাবধারার অগ্রদূত। তরুণ সমাজে এর প্রতিফলন ঘটেছিল ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহী মনোভাবে। এ লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ-সংস্কারের সুরতে অনূদিত হয়েছিল রামমোহন রায় আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে; ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা ও অক্ষয়কুমার দ্ত্ত ছিলেন এর প্রধান ধাত্রী; আর এর সর্বোত্তম সাহিত্যিক প্রতিফলন ঘটেছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের কলমে।
উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পরিস্থিতির বেশ কতকটা বদল ঘটে। ইংরেজি-শিক্ষিত ভদ্রলোকশ্রেণির আকার বাড়ার সাথে সাথে উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ায় সম্মতির হার বাড়তে থাকে। ভিক্টোরীয় জমানার ভাব-স্বভাব ও সংস্কৃতি অনুকরণ-অনুসরণের ক্ষেত্রে কলকাতা অনেক বেশি লায়েক হয়ে ওঠে। কিন্তু একই সাথে প্রবল প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। পশ্চিমায়নের বিপরীতে নিজেদের ‘নিজ’ত্ব ঘোষণার প্রবণতাও ধীরে ধীরে চাঙা হতে থাকে। এই নিজত্বের ঘোষণাটা রাখঢাকহীনভাবে হিন্দুত্বের সুরতে আবির্ভূত হয়েছিল। এতে বিস্ময়ের কোনো ব্যাপার নাই। কলকাতার পুরো আবহটাই ছিল উচ্চবর্ণের, উচ্চশ্রেণির, ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকদের। কাজেই প্রতিক্রিয়ার প্রথম ধাপটা যে কাঁচা হিন্দুত্বের বেশে হাজির হবে, তা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ ‘হিন্দুত্ব’ মোটেই কোনো অনাধুনিক ঘটনা নয়। যেমনটি পার্থ চট্টোপাধ্যায় আমাদের নিশ্চিত করেন, এ জাতীয়তা কিংবা তার রাষ্ট্রকল্প সম্পূর্ণ আধুনিক, এবং নতুন সময়ের পশ্চিমায়িত নির্মাণ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি – একই সাথে নির্মাতা ও নির্মাণ।
এ জমানায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নাকচ হয়েছিল। কালের সাক্ষ্য অনুসরণ করতে পারেন না বলেই আমাদের ভাষ্যকাররা বিদ্যাসাগরের শেষ বয়সের নাস্তানাবুদ দশা ব্যাখ্যা করতে পারেন না; কিংবা এ কালে রামমোহন রায় ও মধুসূদন কেন কার্যত বিস্মৃতির কবলে পড়েছিলেন, তার সুলুক সন্ধান করতে পারেন না। আসলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়েও একই সংকট। বঙ্কিমের হিন্দুত্বকে এক ‘অনাধুনিক’ ঘটনা হিসাবে দেখার কারণেই বঙ্কিম-মূল্যায়নে নানা ধরনের গোলযোগ দেখা দেয়। কেউ কেউ বঙ্কিমের হিন্দুত্ব ও যবন-বিদ্বেষকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন, অপর অংশ এ হিন্দুত্বকে বঙ্কিমের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওইকালের অন্য বিপুল সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীকে রেয়াত দেন। আদতে কালের প্রভাবশালী ডিসকোর্সকে বিবেচনায় নিলে এসব কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা অনেক মসৃণ গতিতে হতে পারে।
আমরা রবীন্দ্রনাথের ‘সময়’কে চিহ্নিত করার জন্য উনিশ শতকের সাহিত্যিক ও ভাবগত সময়ের রবীন্দ্র-পূর্ব কয়েকটি মুহূর্ত চিহ্নিত করলাম। কিন্তু তার মধ্যে দুটি প্রধান কথা বাকি থেকে গেল।
তপন রায়চৌধুরী একটা গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছিলেন ইউরোপ রিকনসিডার্ড (Europe Reconsidered) নামে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে পশ্চিমকে মোকাবেলা করেছিলেন, এ বইয়ে তার বিশদ ফিরিস্তি এঁকেছেন লেখক। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য বেশি জরুরি বইয়ের নামটি। যুগের হাওয়াটাই ছিল এমন যে, বড় লেখক, বড় বুদ্ধিজীবী বা চিন্তকদের জন্য ইউরোপীয় আবহটাকে ভারতীয় আবহে অনুকূল মেজাজে খাপ খাইয়ে নেয়ার চর্চাটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চর্চা। এ কাজ যারা করেননি, তারা কেউই ওইকালের বড় লেখক নন। তুলনীয়, মধ্যযুগের ভারতে বড় লেখকদের অনেকেই ফারসিবাহিত ইসলামি ভাবাদর্শের সাথে সংস্কৃতবাহিত ভারতীয় ভাবাদর্শের সংযোগ-সমন্বয়ের কাজ করেছিলেন। এদিক থেকে বাংলাদেশের সাহিত্যের একটা বড় দিক হয়ত বাঙালিত্ব আর মুসলমানিত্বের সাথে আধুনিকতার নানামাত্রিক আপসরফার প্রস্তাবনা। বাঙালিত্ব আর হিন্দুত্বের সাথে আধুনিকতার নানা কিসিমের আপসরফা বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের যুগেই সম্পন্ন হয়েছে।
তপন রায়চৌধুরী ইউরোপের মোকাবেলার কথা বলেছিলেন। বলেছেন, ভারতের আবহে ইউরোপ আত্মস্থ হচ্ছিল। কিন্তু এর বিপরীত একটা প্রক্রিয়াও চলছিল, যাকে আমরা বলতে পারি ‘ইন্ডিয়া রিকনসিডার্ড’। ইউরোপীয় আবহে ভারতীয়ত্বের মোকাবেলার একটা প্রক্রিয়াও আসলে জরুরি ছিল, যা ছাড়া ইউরোপের মোকাবেলা প্রয়োজনীয় গতি ও গভীরতা পেতে পারত না। ভালো হোক বা খারাপ, ভারতীয়ত্বের এ ধারণাটা মুখ্যত তৈরি হয়েছিল পশ্চিমা প্রাচ্যবাদীদের হাতে, যদিও তাতে ভারতীয়দেরও উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। প্রধানত সংস্কৃতভিত্তিক চর্চার অংশ হিসাবে প্রাচ্যবাদীদের হাতে নির্মিত হচ্ছিল এক ‘সোনালি ভারত’। আর্য-অনার্য সংঘাত নয়, বর্ণবিভাজিত জনগোষ্ঠী নয়, এমনকি দারিদ্র্যপীড়িত বর্তমানও নয়, প্রাচ্যবাদী ভারত ছিল অতীতের এক মনোহর নির্মাণ। কথিত আছে, এ নির্মাণযজ্ঞের প্রাণপুরুষ ম্যাক্সমুলার তাঁর শিষ্যদের ভারত-ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করতেন এই বলে যে, বর্তমান ভারতের অভিজ্ঞতা প্রাচ্যবাদী ভারতের মায়াকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারে। এই বিনির্মিত ভারতের দরকার ছিল; কারণ, এর সাথেই আসলে সংশ্লেষ ঘটতে পারত বিনির্মিত ইউরোপের, যে সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে তৈরি হবে ভারতীয় শিক্ষিত আধুনিক জনগোষ্ঠী।
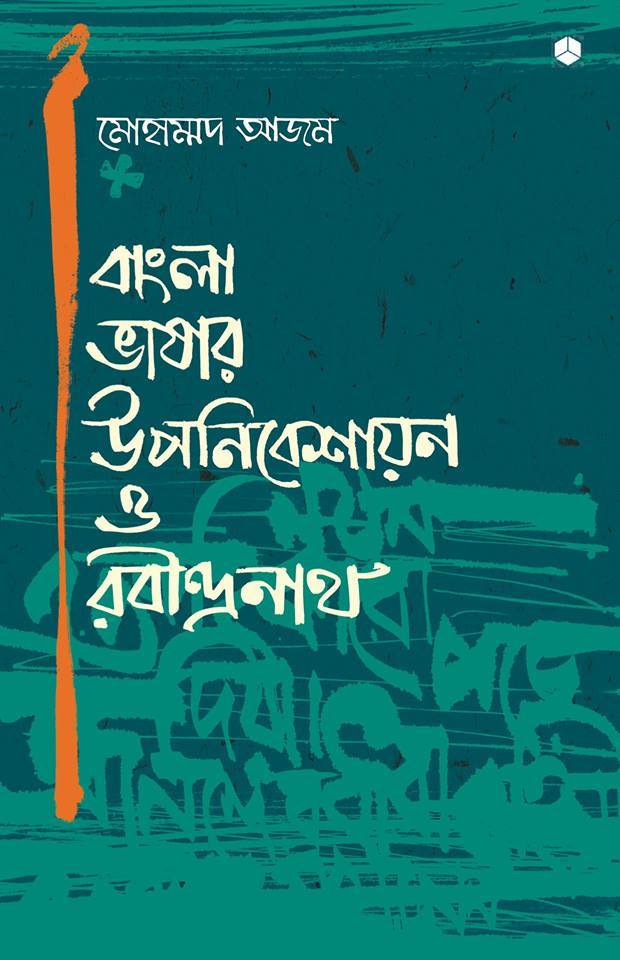
সাহিত্যিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হয়েছিলেন ইতিহাসের এই ‘সময়ে’, যখন ইউরোপের মোকাবেলা প্রায় সাত দশকের চর্চায় একটা নির্ভরযোগ্য ভিত্তি পেয়ে গেছে, আর নতুন ভারতের নির্মাণযজ্ঞও সম্পন্নপ্রায়। এভাবে ভারতীয় বৃহৎ মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রধান চাহিদা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এ দুয়ের মসৃণ সংশ্লেষণ ও সমন্বয়। এ চাহিদার সর্বোত্তম জোগানদার হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এত বড় সাহিত্যিক, আর তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ধর্মিতা। অমিয় চক্রবর্তী যে লিখেছেন, ‘মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর/ পোড়ো বাড়িটার/ ঐ ভাঙ্গা দরজাটা।/ মেলাবেন।’, এবং কবিতার নাম দিয়েছেন ‘সংগতি’, তা রবীন্দ্র-প্রতিভার সবচেয়ে গভীর লক্ষণ। তবে ভারতীয় বহুবিচিত্র বর্ণ-ধর্ম-ভাষার নয়, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা আর অঞ্চলের নয়, তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকর্মে সমন্বিত হয়েছে পুনর্নির্মিত ইউরোপের সাথে পুনর্নির্মিত ভারত; আর এ ভাবেই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন ভারতীয় আধুনিক সংস্কৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসিক হিসাবে।
‘রঙের রবীন্দ্রনাথ’ বইতে কেতকী কুশারি ডাইসন ‘গোরা’ উপন্যাস সম্পর্কে একটা ছোট্ট ব্যক্তিগত উপলব্ধির উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, ‘বিলেতে নৃতত্ত্ববিদ্যার লোকেরা আমাকে কখনও কখনও প্রশ্ন করেছেন, বড় হয়ে ওঠার সময়ে কারা আমার সামনে নারীত্বের role model-রূপে ছিলেন। এর জবাবে তাঁরা সাধারণত প্রত্যাশা করেন সীতা বা সাবিত্রীর মতো চরিত্রের উল্লেখ! আমি তাঁদের বলতে বাধ্য হই, ‘না, রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসের সুচরিতা আর ললিতা।’
ব্যাপারটা বেশ আমোদজনক যে, বিশ শতকের গোড়ায় প্রণীত উনিশ শতকের শেষাংশের নারীমূর্তি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও আদর্শ মূর্তি আকারে অক্ষুণ্ন থাকছে। আমোদজনক, কিন্তু অসম্ভব নয়। কারণ, ভারতীয় মধ্যবিত্তের যে সুরত বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখা গেছে, উনিশ শতকের শেষাংশেই তার ছোট কিন্তু স্পষ্ট একটা আকার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমা ভাব-স্বভাবের সাথে ভারতীয়ত্বের সংযোগ-সমন্বয় ছিল এ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রধান সাংস্কৃতিক সংকট ও চাহিদা। এর জোগান দিতে পারতেন কেবল সেরকম একজন, যিনি ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনকাঠামো ও সম্পত্তিকাঠামোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভোগী, এবং যিনি ইংরেজি ও সংস্কৃতের সম্পদ বেড়ে-ওঠার সাংস্কৃতিক উপাদান হিসাবে নিজের ব্যক্তিত্বে আত্মস্থ করতে পেরেছেন। প্রস্তুতির এ ধরনই রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী অবস্থানে স্থাপন করেছিল। যারা রবীন্দ্র-সাহিত্যে গরিব মানুষের বাস্তবতা কিংবা মুসলমানের জীবন তালাশ করেন, এবং খুঁজে পান বা পান না – তারা দু-পক্ষই আসলে এমন কিছু দাবি করেন, যা রবীন্দ্র-নন্দনের অতুলনীয় সৌধের অতি প্রান্তীয় অথবা বাইরের জিনিস।
প্রশ্ন হল, নান্দনিকতার কোন কোন অভাবনীয় এনতেজাম রবীন্দ্র-সাহিত্যকে এমন অসামান্য দায়িত্ব পালনে সমর্থ করেছিল। প্রধান দুটির উল্লেখ করা যাক। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন লিবারেল হিউম্যানিস্ট – কথাটার পশ্চিমা অর্থেই – আর কলোনিয়াল পরিস্থিতিতে কথাটার যতটা উদারনৈতিক রূপ কল্পনা করা সম্ভব, রবীন্দ্র-সাহিত্যে তার সবটারই প্রতিফলন দেখি। পুনর্নির্মিত ভারতের সাথে পুনর্নির্মিত ইউরোপের মসৃণ সমন্বয়ের জন্য চরমপন্থামুক্ত এ দৃষ্টিভঙ্গি আবশ্যক ছিল। দ্বিতীয় গুণ তাঁর কল্পনাপ্রবণ সুদূরতা তথা রোমান্টিকতা। সৌন্দর্য, রুচি ও কল্যাণবোধের যে অমিত উৎপাদন রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান গুণ, তার জন্য সুদূর ইউরোপ আর সুদূর অতীত ভারতের কল্পনাপ্রবণতা আবশ্যক ছিল – বর্তমানের দীনতা এড়িয়ে যা ভবিষ্যতের আদর্শ সুরত প্রস্তাব করতে পারবে।
সময়কে এভাবে ধারণ করতে পারাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান সম্পদ।